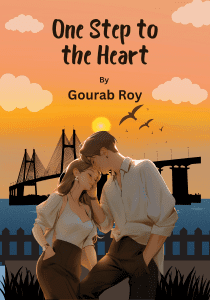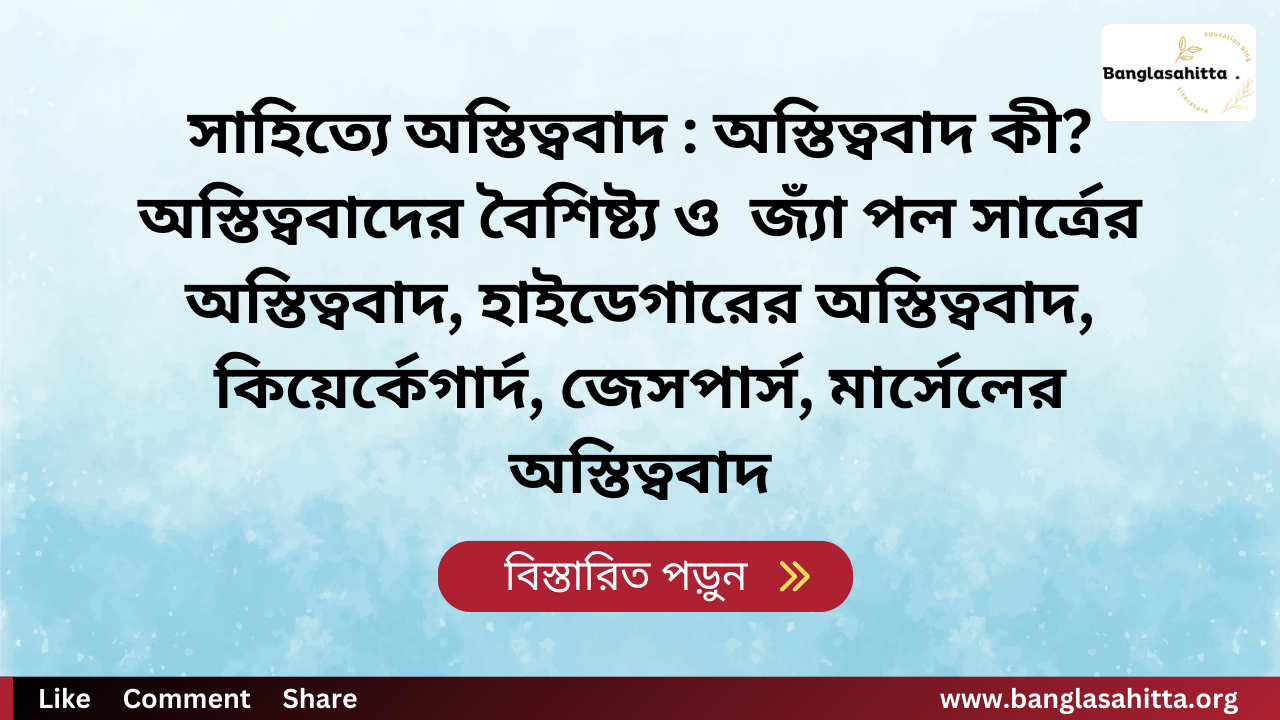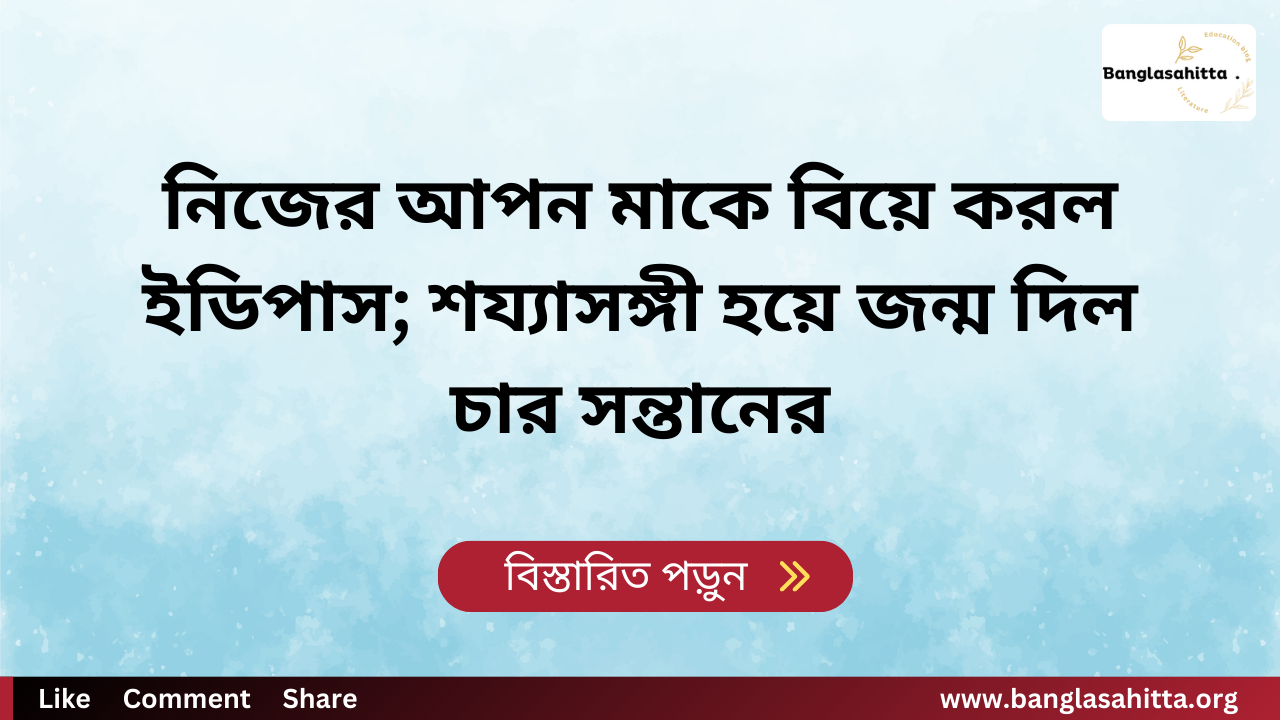যেতে নাহি দিব:
এ যেন একজনের কথা নয়, এটি একটি শাশ্বত বার্তা; এটি যেন অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘We are Seven’ কবিতাতেও একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের ‘অতিথি’ গল্পের নায়ক তারাপদর সঙ্গে এই কবিতার বালিকার মিল রয়েছে। এ যেন ক্ষণিকের অতিথি, যেমন নদী আপন বেগে পাগলপারা হয়ে যায়; কোনো বন্ধনই যেন একে আটকে রাখতে পারে না। কোনো বিষাদ বা ক্রন্দনকে যেন যে মানে না, জীবন যে চির চলিষ্ণু, সে এগিয়ে চলে নতুন নতুন পথে। পৃথিবী নিজেই যাযাবর। তাই পৃথিবীর মতো তার সব জীব কোনো স্থানে স্থির থাকে না। এ যেন কবির চিরকালের মানসসুন্দরী। তিনি চান, এই মানসসুন্দরী তাকে আকৃষ্ট করুক। কিন্তু তিনি স্থায়ী নয়, তাই তিনি যে আহ্বান উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেন অনন্ত কালের অজানা পথে।
ঝুলন কবিতার বিষয়বস্তু:
‘ঝুলন’ কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১২৯৯ সালে, ১৫ চৈত্রে, এবং ‘সমুদ্রের প্রতি’ কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১২৯৯ সালে, ১৭ চৈত্রে। তাই এই দুটির মধ্যে প্রভাবের উৎসটা একই। সমুদ্রের বিষয়বস্তু এদের মধ্যে খুবই গূঢ় মিল রয়েছে। ‘সমুদ্রের প্রতি’ কবিতায় বাইরের সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, ঝুলন কবিতায় অন্তরের সমুদ্রের কথা রয়েছে। এই বাইরের ও ভিতরের কথা হল কবির বাহিরের ও ভিতরের প্রতিফলন।
রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ঝুলন উৎসব থেকেই এটি প্রেরণা পেয়েছে। এটি কেবল উৎসব নয়; এটি কবির অন্তরের অনুভূতির প্রবাহ। মানস দেবতার সঙ্গে তার নিত্য অন্তরের সম্পর্ক এই ঝুলনে প্রকাশিত হয়েছে। রাতের অন্ধকার দেখে কবির মনে হয়েছে যেন তার মৃত্যুর সময় এসেছে। কবি বুঝেছেন, এটি যৌবনের সেই মাদকতা, যা উন্মাদনা সৃষ্টি করে; এ চুপ করে বসে থাকার নয়। কবির প্রাণ আজ উন্মাদ। কবির তবুও স্বপ্নভরা দিন আছে, তার জীবনে যেন দোলা লেগেছে। বারবার তার মনে হয়েছে, এ প্রাণ যেন চলে গেল। তিনি জীবনকে ভালোবাসেন, এই জীবনকে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন চিরকাল। তার প্রাণ এতদিন সযত্নে ছিল, কিন্তু আজ সে প্রাণ বাইরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, কবি এতে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এটি কেবল তার জৈবিক প্রাণ নয়, এ তাঁর অন্তর দেবতা, যার জন্য তিনি বহুদিন ধরে বসে আছেন। আজ তাকে তিনি মেতে উঠতে দেখেছেন, তার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এই তাঁর বেদনা, এই তাঁর Cosmic Imagination; ‘পরশ পাথর’ জীবনের কাছে কবির প্রশ্ন—এ যেন কবির কাছে চিরকাল থাকে।
মানুষ জীবনের প্রতি মুহূর্তে নিজের ভিতরে নিজেকে খুঁজে চলে। এই অম্বিষ্ট সত্তা তাঁর জীবনে নানা বিচিত্রতায় সৃষ্টিমুখরতায় প্রাণশ্বাসে দেখা দেয়, কিন্তু সবসময় ধরা দেয় না। যখন সে ঘুমিয়ে থাকে, তখন এক অন্ধকার রূপ তার জাগরণে সৃষ্টি সুখের উল্লাস। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে তাঁর জীবনে চিরকাল এক প্রেরণায় এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কখনও তার প্রিয়া রূপে, কখনও প্রকৃতি রূপে, কখনও প্রেম রূপে, কখনও তার ক্রিয়া রূপে এসে দেখা দিয়েছে। কবি কখনও তাকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছেন দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্ত রাখতে। তার সোহাগে, স্নেহে, অলস আবেশে তাকে নিয়ে কেটেছে কত দিন রাত। কিন্তু একদিন তার মনে হয়েছে, এভাবে জীবনযাপন বৃথা। প্রলয়ের বীণায় বাণীর ঝংকার যখন বাজবে, মৃত্যুর আহ্বানে নতুন জীবনের আবেদন যখন উন্মোচিত হবে, তখন তো কবিকে এই প্রাণশক্তিকে জাগাতেই হবে। বৃথা কালযাপনে তাই কবি রাজি হন। ঝুলন কবিতায় কবি এই দ্বিধাবিভক্ত সত্তার জীবনান্তরে উপস্থিত জীবনান্তরের প্রস্তুতিতে প্রাণমুখর ঝুলন খেলার বর্ণনা দেন। এ খেলার একদিকে কবি, আর একদিকে তার প্রাণশক্তি, তার জীবনবধূ, তার আজন্ম ভালোবাসার প্রিয়ারের প্রতিমা।
বাইরের বর্ষা বহুবার কবিকে অন্তরমুখে জাগিয়ে তুলেছে। বাইরের পৃথিবীর তুমুল প্রলয় কবির অন্তরের পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছে বারবার। ঝুলন কবিতাতেও এরকমই এক বর্ষার রজনী প্রেক্ষাপট বর্ণিত। সেদিনের সেই রাত্রিবেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বের দিকে তাকিয়ে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে দেখে কবির মনে হয়েছে, আজ তার অন্তরলোকেও একই সুর বেজে উঠেছে। ঝটিকার উদ্দাম আহ্বানে কবির সুপ্ত প্রাণ জেগে উঠে কবিকে তার অলস স্বপ্ন শয়ন ত্যাগ করতে ডাকে। কবি বুঝেছেন, যেই প্রিয়াকে, যে প্রাণ বধূকে নিশিদিন বহু অনুরাগে রুদ্ধ দ্বার কক্ষে বাসর শয়ন রচনা করে সযত্নে রেখেছিলেন, যাকে নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে কত মধুর সংগীতে ঘুমে জাগরণে নিবিড় বন্ধন সুখ অনুভব করেছিলেন, আজ এই ঝঞ্ঝা প্রমত্ত রাত্রির নতুন খেলায় তার সঙ্গে নতুন করে হিসাব মেলানোর পালা। বিগত দিনের প্রেমরক্ত কুসুম পাপড়িগুলি শুধুই ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি চারিদিকে। আজ রাতে কবিকে নতুন করে এই প্রাণশক্তির সঙ্গে, এই অতি অন্তরতম প্রিয়ার সঙ্গে মরণদোলায় ঝুলন খেলায় মেতে উঠতে হবে। সুখে অলস মুহূর্ত। অতিবাহিত, স্বপ্নে জড়িমা ভেঙে খানখান। সোহাগ নিদ্রিত অন্তর প্রিয়া প্রলয়লোকের আহ্বানে জেগে উঠছে কবির শোষিত দুরন্ত হিল্লোলে দুর্বার কল্লোলে। কবিও তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আজ সমস্ত আবরণ ছিন্ন করে তার সঙ্গে মুখোমুখি বসতে তিনি রাজি। প্রাণের সঙ্গে কবি নতুনসত্তার এই সাক্ষাতকালই সৃষ্টির আবৃত রহস্য অনাবৃত করে। বাইরের পৃথিবীতে উন্মাদ প্রকৃতিতে কবি আজ নিজের অন্তরে এই জীবনমরণ ঝুলন খেলায় প্রেরণা পেয়েছেন। কবি তো চির সৃষ্টি মুখর। অতীতকে কিছু বোলে নতুনের দিকে নিত্যযাত্রী। জীবনমরণের এই ঝুলন খেলায় কবি জানেন, এই নতুন প্রাণ আবিষ্কৃত হবেই হবে।
সোনার তরী কবিতার বিষয়বস্তু:
১২৯৮ সালের আষাঢ়ে সাজাদপুরে বসে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলার নদীমাতৃক পল্লিভূমির জীবনের মধ্যে এক চিরন্তন ও মহৎ অনুভূতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতির সেই প্রসারিত উদাসীনতার মধ্যে বয়ে চলা মানুষের জীবনের নিশিদিনের কর্মস্রোত কবির কাছে অত্যন্ত নিষ্ফলভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সেদিন সেই নিরুদ্দেশ প্রকৃতির শাস্তিময় ঔদার্যে নির্বিকার সৌন্দর্যের দীপ্ত প্রদীপ উন্মনা হয়ে গেছেন তাঁর চারপাশের পৃথিবীর নিত্য ক্ষুদ্রতার জর্জরিত অশাস্তির পাড়ে গিয়ে। সোনার তরী কবিতার মধ্যে এই পরিবেশ পুরোপুরি না পাওয়া গেলেও এক ভাবসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ কবিতার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন বেশ কয়েক জায়গায়। কবি নিজেই জানিয়েছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে লিখিত একটি চিঠিতে যে সোনার তরী কবিতার কল্পনা বর্ষায় পরিপূর্ণ খরবেগে বয়ে চলে পদ্মার উপর বসে। ভরা পদ্মার বাদল দিনের ছবি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল, যদিও বেশ কয়েক মাস পরে ফাল্গুনে। কল্পনা ও রচনার এই কালগত ব্যবধানের অসংগতিও কবিকে পীড়িত করেছে। তাই তার মনে হয়েছে, সোনার তরীর যে ইতিহাস সত্য তা বিগত দিনের ইতিহাস। যেদিন তার প্রকাশ, সেদিনটি নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। আসলে এই কবিতার সঙ্গে জন্ম রোমান্টিক কবির অনুভূতির এক আত্মিক সম্পর্ক আছে। মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা মানুষকে কীর্তি এনে দেয়। তারই দূরবীনে চোখ লাগিয়ে মানুষ কল্পিত ভবিষ্যতকে অমর করে রাখতে চায়। অথচ মহাকাল এই বিরাট পৃথিবীর জীবন নদীতে যে তরীখানি বেয়ে নিয়ে চলেছে, তাতে কীর্তিমানের চেয়ে কীর্তি বেশি। সাজাদপুর থেকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে কবি বলেছিলেন, “মানুষ সেখানে আপন সকল কাজকে সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে—আপনার সকল ইচ্ছা চিহ্নিত করে রেখে দেয়—পাস্পারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে। জীবনচরিত লেখে এবং মৃতদেহের উপর পাষাণের চির স্মরণ গৃহ নির্মাণ করে। তারপর অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্তৃত হয়; সময়ের অউনার এটি কারোর খেয়ালে আসে না।”
শিলাইদহ পর্ব
শিলাইদহ পর্বে এসে কবি বাস্তব জীবনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে গেছেন। মানুষের কর্মসাধনার সঙ্গে কবির যোগ ছিল অটুট এবং নিরন্তর। কিন্তু এই সময়েই কবি তার কল্পনার রাজ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। যখন কর্মজগৎ আর কল্পনার জগৎ পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কবি বুঝতে পারেন জীবনের এবং দুস্তর ব্যবধান তার চারপাশে গড়ে উঠছে। কবি নিজেকে এই কর্মজগতের একজন সদস্য হিসেবে অনুভব করেন। জীবনভর তার সাধনার ফলাফল তিনি তার নিজের কর্মভূমিতে ফলিয়েছেন। যখন তিনি পাস্পারিত্বের দিকে তাকান, তখন বুঝতে পারেন যে এই জীবনপর্বের শেষে একদিন সঞ্চিত ফসলের হিসাব মেটাতে এসে বিষাদে ভরে যাবে। একটি ভরা নদী আপন গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, তবে কবি একা হেঁটে চলেছেন তার ছোট্ট খেতের দিকে। এ একাকিত্ব চিরকালীন; তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের চারপাশে একটি তলহীন এবং সীমাহীন ব্যবধান রয়েছে। সেই ব্যবধানের মধ্যে মানুষ কাজ করে চললেও তাকে অতিক্রম করতে পারে না। তার বিষণ্ণতা তাকে নাড়া দেয়, কিন্তু তার মুছিয়ে দেবার সাধ নেই।
অবশেষে যখন জীবনের পথ প্রান্তে এসে মেশে, তখন তিনি দেখতে পান কোনো এক কাণ্ডারী নৌকা বয়ে চলেছে, ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে। তার গানের সুরে ভরা পালের নৌকায় কবি বুঝতে পারেন যে এ কাণ্ডারী তাঁর চির পরিচিত। কবির কাছে জীবনব্যাপী সাধনা একটি সোনার তরণীর মতো, তবে সেই তরণী সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকেও ঠাঁই দিতে চান। কিন্তু এখানেই স্থান সংকুলান হল না। সোনার ধান ধরেছে সোনার তরীতে, কিন্তু সেই ধানের চাষি তার শূন্য খেতের পাশে একা পড়ে থাকলেন। মানুষের জীবনের অর্জিত সাধনার ধন মহাপৃথিবীর তরণীতে নিত্য জমা হতে থাকে, কিন্তু এই ধন যারা সৃষ্টি করেছে তাদের কথা কেউ মনে রাখে না; অথচ তারা চায় বেঁচে থাকতে। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিস্মৃত ইতিহাস কেবল তাদের কীর্তির মধ্যে সাধনার মাঝে অমর হয়ে আছে।
বীরেশ্বর গোস্বামীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি বলেছেন— “মানুষের এই একটি ব্যাকুলতা। এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে এই ব্যথা আছে। আমাদের সেবা, আমাদের প্রেম— আমরা দিতে পারি। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে দিতে গেলে সেটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা প্রীতিদান করব, কর্মদান করব, কিন্তু পালিয়ে যাব না, ইহাই জীবনের শিক্ষা।”
বাস্তবিক, সংসার মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম ও কর্মফলকে সযত্নে রক্ষা করে, কিন্তু তার সঙ্গে কর্মকর্তাকে আলাদা করে রেখে দেয় না। যখন মানুষ সংসারের নৌকাকে তার জীবনলব্ধ ফসল দিয়ে ভরিয়ে দেয়, তখন সে চায় যে তার চিহ্নটুকু যেন সেখানে থাকে। কিন্তু এই চলমান মানব পৃথিবী যে অনন্ত যাত্রার পথে নেমেছে, সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি লিখেছেন পূর্বক চিঠিতে— “আমি তাহাকে বলি, ‘ওগো, তুমি আমার সব লও এবং আমাকেও লও। সে আমার সব লয়, কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে, তাহা কি আমরা জানি? সে যে অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে। তাহার কুল কি আমরা দেখিয়াছি? কিন্তু তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিণত অথচ মানব সংসারকে আমাদের যাহা কিছু সমস্ত কিছু দিয়া যাইতে হইবে। নিজেতো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না, নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।”
অতৃপ্তি ও কাব্য
যে অতৃপ্তি বোধ তার অধরায় অন্বেষা রোমান্টিক কবির স্বভাব বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র কাব্য জীবনে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা পর্বে তার বর্ষণ সহজলভ্য। সোনার তরী কবিতাটি এই রোমান্টিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ। যে মানসসুন্দরী তার জীবনের নৌকাখানি বেয়ে চলেছেন, কবি চান সেখানেই তার যেন নিত্য স্থান হয়। অথচ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কবি শঙ্কিত— হয়তো এই প্রাপ্তি তার জীবনে ঘটল না, যাকে তিনি একান্ত আপন করে চান, তাকে তিনি পাবেন কিনা, এ শঙ্কায় তিনি দোলাচল। তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে কবি অপেক্ষা করে আছেন এই জীবন দেবতার চরণে পরিপূর্ণ সমর্পণের জন্য। কিন্তু এই বেদনাই অহরহ আজ কবির চারপাশে মূর্ত হয়ে উঠছে যে সেই সোনার তরীতে হয়তো তার জায়গা হল না। এক নিঃসীম নিঃসঙ্গতায় কবির হৃদয় ভরে ওঠে। এক অতন্ত্রীয় বিরহে তিনি আত্ম হয়ে ওঠেন। আর সোনার তরী এই আত্ম অতৃপ্তিতেই ভরে আছে।
বৈষ্ণব কবিতা
বৈষ্ণব পদাবলীর এক ভক্ত পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতায় লেখার অনেক জায়গায় বৈকবিদের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি আছে, আছে পরোক্ষ প্রভাব। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ বা ভক্তি কোনো ভাবেই মহাজন বৈবেদের সাধনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কবি প্রেম, তাঁর জীবনের সাধনা, এর সাধ্য এই বিশ্বে প্রকৃতির মাঝে মানুষের সংসারে ভালোবাসার যে অনন্ত ধারা নিঃশব্দে নিরবে বয়ে যেতে দেখেছেন, তিনি তারই অমৃত রসসিঞ্চনে তিনিও ধন্য ও কৃতার্থ। সে ভালোবাসায় নন্দনলোকের দিব্য সৌরভ মিশল কিনা, দেহ ইন্দ্রিয়অতীত, স্বর্গীয় মহিমায় অভিব্যক্ত হল কিনা, এই নিয়ে তিনি চিন্তা করেননি। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমমুখর গানগুলিকে তিনি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের ভগবগীতি রূপে মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাঁর কাছে সেগুলি জীবনের গভীরতম উৎস থেকে বেরিয়ে আসা সবচেয়ে পুরাতন, অথচ সবচেয়ে শাশ্বত বাণী। ‘বৈষ্ণব কবিতা’য় এই মূল বক্তব্যটিকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন কবি।
মানুষের সংসারে তার নিত্য প্রবহমান কাব্যধারার মধ্য দিয়ে জীবনের শতসহস্র সুখ দুঃখ উত্থান পতনের মধ্য থেকে একটি অঙ্গসুর চিরকালীন তাৎপর্য নিয়ে জেগে থাকে। সে তাৎপর্য অঙ্কিত হয়ে আছে মানুষের মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, প্রেম-বেদনার সঙ্গে। এতেই মানুষ চরম দুঃখেও হারিয়ে যায় না। দুরন্ত অবসাদেও বেঁচে থাকে, বিরহের মধ্যেও খুঁজে যায় নতুন জীবনের আলো। এ হল মানুষের জীবনের আদি প্রাপ্তি, শেষহীন সঞ্চয়। এই তাঁর প্রেম। একে সে অনুভব করে আপন অন্তরের স্তরে স্তরে অন্যের জীবনের সঙ্গে মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণে। কবির মনে হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এই নিত্য প্রেমের অক্ষুণ্ণ জয়ধ্বনি। রাধা-কৃষ্ণের জীবনের পারস্পরিক সেই প্রণয়লীলার মধ্যেই দীনমর্ত্যবাসী দিনরাত প্রণয় পিপাসা মিটবেই, এই ছিল কবির বিশ্বাস। যে বৈকুণ্ঠ মানুষের পৃথিবী থেকে অদৃশ্য, কোনো আলোকলোক যার ঠিকানা, কেবল তারই উদ্দেশ্য— মানুষেরই তৈরি গান এ ধরণির ধুলার থেকে উদ্ভাসিত হয়ে বেজে যাবে, অথচ যার সে গান গাইল আর শুনল, তারা তার মাধুর্য উপভোগ করতে পারবে না, এতো হতে পারে না। তাই বৃন্দাবনের নিসর্গকুঞ্জে তারিখ না পাওয়া কোনো অতীতে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান অভিমান, যে লীলা শ্রাবণ রজনিতে কালিন্দীকে সাক্ষী রেখে অভিনীত হয়, শুধুমাত্র দেবতার চরণে তার রূপরসগন্ধ অর্পণ করা হয়নি। যে গোত্র রক্ষিত আছে অনন্তকালের প্রেমপিয়াসী অযুত নরনারীর জন্য। সেদিনের সেই তরুণ বসন্তে যে গীত উৎসব বর্ণে, সুরে, গন্ধে, দিকদিগন্ত আমোদিত করে তুলেছে, তার প্রতিটি কণা অনস্থর হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিনের কবিকে তাই এ যুগের কবি জিজ্ঞাসা করেছেন— রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার সেই মধুঝরা ছবিখানি কবির আঙিনার থেকে তুলে রাখা হয়েছে কিনা? রাধিকার ছলছল অশ্রু আঁখি, চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা কি কবি তাঁর পর্ণকুটিরে নিভৃত থেকেই আবিষ্কার করেননি?
বাস্তবিক, মানুষ চিরকালই একই ফুল রেখে দিয়েছে সকলের জন্য। দেবতার চরণে যে অর্ঘ্য, যে অঞ্জলি, দেবতার কণ্ঠে যে প্রেমের পুষ্পহার— যে নিজের হাতে পরিয়ে দেবে বলে তৈরি করেছে নবীন ফাল্গুনে বিজন বসান রাতে মিলন শয়নে, তাই তো সে পরিয়ে দিয়েছে তার বঁধূর গলায়। তার সেই আবছা আলোয় ভরা মিলন কুটিরে তার অন্তরের আপনজনই যে দেবতা, স্বর্গলোকের অমর দেবতা, যে তার অতিপরিচিত জনের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে চিরকাল। তাই বৈষ্ণব কবি অনন্ত প্রেম মিলনে গান আসলে প্রতি চিরকালের মানুষের জন্য, যে মানুষ প্রেমপূজারি, যে মানুষ প্রেম কাঙাল। কবি বিশ্বাস করেন, এই প্রেম যেমন ঊর্ধ্বলোকে দেবমন্দিরে বন্দনাগীতিতে অবারিত হয়, তেমনি মিলন কক্ষে প্রিয়জনের কাতর দৃষ্টিপথেও সজল আশ্লেষে নামাঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব কবিরা এই সর্বোপরি শাশ্বত প্রেমের কবি। রবীন্দ্রনাথও সেই একই প্রেমের পূজারি। প্রেমকে তিনি ভাগে ভাগ করতে পারেন না, কারণ যে সে অখণ্ড, অনন্ত এবং অনন্য।
বসুন্ধরা কবিতার বিষয়বস্তু:
বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরের একটি গভীর যোগ রয়েছে। তিনি এই প্রকৃতিকে নিখাদ ভালোবেসেছেন এবং এটিকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সৌন্দর্যের যে ঢেউ উচ্ছ্বাসিত হচ্ছে, তা কবিকে প্রবলভাবে মুগ্ধ করেছে। আবার, মানুষের কর্মধারার যে সহস্র প্রয়োজন সভ্যতার সোনালী দরজা থেকে অন্য সোনালী দরজার দিকে ধেয়ে চলছে, সেটাও কবির অন্তরের প্রাণের আনন্দকে উজ্জীবিত করেছে। পৃথিবী তার সুরূপ, শব্দ এবং স্পর্শ নিয়ে কবির কাছে প্রেয়সীর মতোই স্নেহশ্রয় জোগাচ্ছে, যেন তিনি অকর্মা অবস্থায় আছেন। নিজেই কবি বলেছেন—
“আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনই।”
(ঐকতান)
এমন সম্ভবত কারণেই বসুন্ধরার সুধাপাত্রে যত রস ফেনায়িত হয়ে উঠেছে, যত সংগীতে কল্লোলিত হয়েছে, কবির জীবনযাত্রার হৃদয় বীণার তারে সেই সঞ্চয় ধরা আছে। কবি নিজের রুদ্ধ হৃদয়ে অন্ধকার পথ ভেঙে, চারপাশের সংকীর্ণ অচলায়তন উন্মুক্ত করতে চান, তাই তিনি ভূলোকের প্রান্ত থেকে প্রান্তে, দিক্ দিগন্তে ছুটে চলেন। গৃহের কোণে বসে, গ্রন্থপাঠরত কবি মানসলোকে কল্পনার পৃথ্বীরাজে চড়ে, দেশ-দেশান্তরে নিঃকলঙ্ক নিহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে নিজেকে দাঁড় করাতে চান। পৃথিবীর কোণে কোণে কত বিচিত্র সভ্যতা, কত বিচিত্র ইতিহাস, কত বিচিত্র জনগণ ছড়িয়ে আছে। মরুভূমিতে, দুর্গম স্বাধীন আরব সন্তান, তিব্বতের গিরিতে শান্ত বৌদ্ধ মঠ, নির্ভীক নবীন দীপ্তি, প্রবীণ কর্মমুখর চিন—সকলেই কবির কল্পনার অপাবৃত চোখে ধরা পড়েছে। এ পৃথিবীতে কবির অন্তরের প্রিয়া যুগ-যুগান্তর ধরে অজস্র দিনরাত্রি ব্যাপ্ত করে কবির অন্তরলোকে তার ফুলের সাজি ফুটিয়েছে, অপূর্ব গন্ধ জাগিয়েছে। পদ্মাতীরে একাকী আনমনা কবি, অন্তরের গোপন প্রদেশ থেকে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে।
তার জীবন রসধারায় এক অন্ধ আনন্দের মহাব্যাকুলতা জেগে উঠে। কবি অনুভব করেন, পৃথিবী তাকে ডাকছে। তার কর্মময় খেলাঘরে এখন কবির নিয়ন্ত্রণ। দূরে পৃথিবীর দিগন্তরেখায় যখন সন্ধ্যা নেমে আসে, যখন জ্যোৎস্নায় অপরিস্ফুট শাস্ত রশ্মিরাশি আকাশকে ধীরে ধীরে আবৃত করে, তখন কবির অন্তরের সুপ্ত আনন্দ নতুন প্রাণের সুরে নতুন নৃত্যের চপল ভঙ্গিমায় নিখিলের বিচিত্র আনন্দধারায় মিশে যেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কবির বিশ্বাস, তার এই অনুভূতি বিশ্বমানবের নিত্যকালের অন্তরের কথা। জগতের যত প্রেমিক, যত নর-নারী, বর্ষে বর্ষে কবির এই প্রেমরক্ত আনন্দের ভাষায় তাদের জীবনের ভাষা খুঁজে পাবে। তাঁদের যৌবনে বসন্তের দিনে কবি বেঁচে থাকবেন এই উন্মুখ প্রেমের অঙ্কুর রূপে। সমস্ত প্রাণীই এই জাগরণ পূর্ণ জীবনের সমাজে কবির নিত্যকালের বসতি। এই যে পৃথিবী আজ রস ও রূপে অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেটি আসলে কবির জীবনই; যার কখনও প্রিয়া, কখনও জননী, কখনও প্রেয়সী। কবি মগ্নচিত্তে থাকে, কখনও তার শ্রেয়সীরূপে অম্লান মহিমার আশ্রয় খোঁজে।