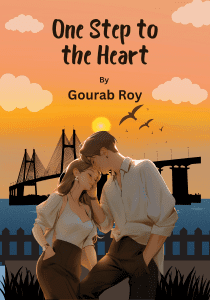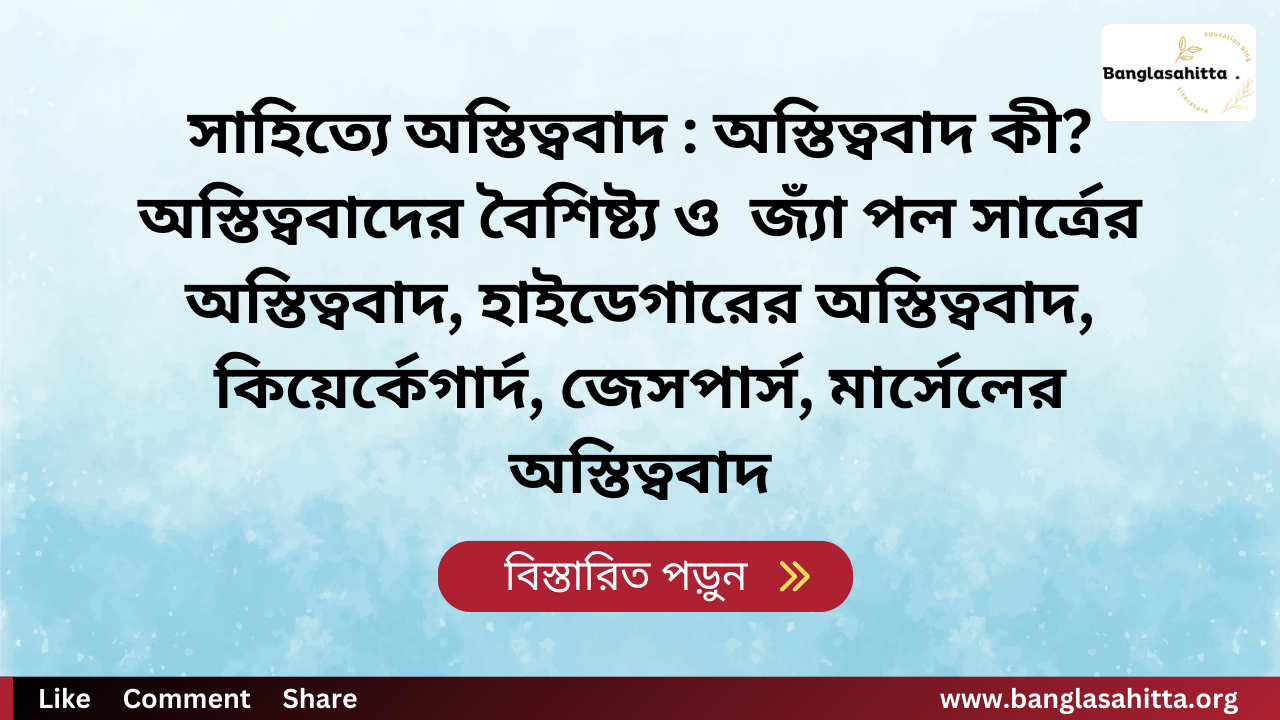বাংলার মহিলা কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা না হলেও স্বীয় প্রতিভার দ্বারা মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) বাংলা সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট কবি-লেখিকার স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। জন্মসূত্রে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন এবং তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় মাইকেলের প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। তবে তিনি রবীন্দ্র-সমকালীন কবি হওয়ায় যুগধর্মের প্রভাবে গীতিকবিতার ধারায় ক্রমে প্রবাহিত হতে থাকেন। তাঁর কৃতিত্ব শুধু কাব্য-রচনায় সীমাবদ্ধ নয়; মানকুমারী গদ্য-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাতেও লিখেছেন।
প্রথম জীবনে পিতৃকুল এবং পরবর্তী জীবনে স্বামী সান্নিধ্যে সাহিত্য রচনায় বিশেষ উৎসাহ লাভ করেছিলেন মানকুমারী। তাই অতি অল্প বয়সে, মাত্র ১৪ বছরে, তিনি ‘পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা’ নামক একখানি কবিতা রচনা করেন যা সেকালের প্রখ্যাত সাময়িকপত্র ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত হয়। কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং তখন মানকুমারী মধুসূদন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, ফলে এতে বীররসের প্রাধান্য দেখা যায়। কাব্য রচনার পূর্বেই মাত্র দশ বছরে তার বিবাহ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুড়ি একুশ বছর বয়সে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। স্বামীর অকালমৃত্যু কবির মনে গভীর বেদনা সঞ্চার করে, যার ফলস্বরূপ মানকুমারী ১৮৮৪ খ্রীঃ রচনা করেন ‘প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রেম’—এটি গদ্যপদ্যাত্মক রচনা। এই কাব্য কবির বেদনা ও শোকের অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটায় এবং শোককাব্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে।
যেই কালে মানকুমারী জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে একদিকে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের প্রভাবে কাহিনীকাব্যের ধারাটি সচল ছিল, অন্যদিকে বিহারীলাল ও তাঁর অনুসারী শিষ্যদের আবির্ভাবে গীতিকাব্যের ধারাও ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছিল। ফলস্বরূপ, মানকুমারীও ওই দুই ধারার টানাপোড়েনে পড়েছিলেন। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীররসাত্মক কাব্যরচনা করার পর তিনি আবার গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকেন। এর ফলস্বরূপ, তার গীতিকাব্য ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ (১৮৯৩) এবং ‘কনকাঞ্জলি’ (১৮৯৬) প্রকাশিত হয় এবং পূর্বধারার অনুবর্তন রূপে ‘বীরকুমার বধ কাব্য’ (১৯০৪) প্রকাশিত হয়।
উল্লেখযোগ্য যে, মানকুমারীর প্রতিভা শুধু কাব্যরচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি গদ্যরচনায়ও যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন, যা সমকালের ইতিহাসে প্রমাণিত। তিনি ‘বামাবোধিনী’ প্রভৃতি সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ রচনা করে পদক লাভ করেন এবং ছোটগল্প রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ‘কুন্তলীন পুরস্কার’ লাভ করেন। এছাড়াও, তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতির নিদর্শন হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক’ (১৯৩৬), ‘জগত্তারিণী সুবর্ণপদক’ (১৯৪১) এবং ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করেন।
মানকুমারী বসুর সাহিত্যকৃতি ও প্রতিভার বিশ্লেষণে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেনঃ “মানকুমারী এমন সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারা ক্রমবিস্তৃতি লাভ করছে এবং আখ্যায়িকা ধারারও প্রভাব রয়েছে। মানকুমারীর রচনায় এই দুটি ধারার যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তার ‘প্রিয়প্রসঙ্গ’ একান্তভাবে শোকগাথা। কবির বৈধব্যযন্ত্রণার নিরাভরণ প্রকাশ এতে ঘটেছে। অন্যদিকে, ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ এবং ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থে প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের সহজ সরল অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাঁর অনেক কবিতাতেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিষন্নতা প্রতিফলিত হয়েছে। মহাভারতের বীরকুমার অভিমন্যুর মৃত্যুকাহিনী অবলম্বনে রচিত ‘বীরকুমার বধ’ আখ্যায়িকাটি বীররস ও করুণরসের মিশ্রণে হলেও, তার পিতৃব্য মধুসূদনের প্রভাব থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, কাব্যটি রসাসক্ত নয়। গীতিকবিতায় মানকুমারীর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দেখা যায়, কিন্তু আখ্যায়িকায় তার অভাব বিদ্যমান।”
বাংলা কাব্যসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান ও কৃতিত্ব
রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য ছন্দের যাদুকর বলে সুপরিচিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২- ১৯২২ খ্রীঃ) স্বীয় প্রতিভা বলে রবীন্দ্রনাথের জীবকালেই কাব্য রচনা করে প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন-শুধু এই কথা বললে তার প্রতি মােটেই সুবিচার করা হয় না। কারণ, তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বভাবতঃই তিনি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত হবেন, এটাই অতিশয় প্রত্যাশিত হলেও কাব্যরচনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ধারার পথিক এবং শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কোন কোন বিশিষ্ট কবিও এক সময় তার পস্থাই অনুসরণ করেছিলেন-সত্যেন্দ্রনাথের এই কৃতিত্বই তাকে রবীন্দ্র যুগেও একটি নামে চিহ্নিত করেছিল। ব্যক্তি জীবনে তিনি নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ও জ্ঞানমার্গের তপস্বী মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের মানসিক গঠন ছিল এমনই যা কবি-কল্পনাকে কখনাে লাগাম ছাড়া হাতে দেয়নি। ফলতঃ যথার্থ কবি-প্রকৃতির অধিকারী তিনি ছিলেন না বলাই বােধ হয় সঙ্গত। এ বিষয়ে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন- “সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানস বহু-বিচিত্র আপাত-বিরােধী মানসিকতার আশ্রয়-ভূমি। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কাছে এসেও তিনি সবচেয়ে বড় অ-রাবীন্দ্রিক—এইখানেই তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র আস্বাদন-বৈচিত্র্য।”
রবীন্দ্রপ্রভায় বর্ধিত কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের জন্য বিশিষ্ট আসন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই অনুজপ্রতিম কবির অকাল মৃত্যুতে ‘পূরবী’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত’ কবিতাটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন –
‘জানি, তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীতের ভালোবেসেছিলেন। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার ‘পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছে ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ, কোমল। তুমি ব্যঙ্গ ভারতীয় তন্ত্রী পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলেন পারাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুরে কখনো ধ্বনিবে মন্ত্র রবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।’
রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্য-গগনে তখন তার একদল অনুরাগী তার আদর্শে ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রায় অন্ধভাবেই অনুসরণ করেছিলেন, আর একদল অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র প্রভাব-বর্জিত সাহিত্যই শুধু রচনা করেন নি, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র পথের পথিক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন—প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মােহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম। জনপ্রিয়তায় এদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামই প্রাগবর্তী বিষয়বস্তুর দিকে যেমন, তেমনি ভাষা ছন্দ এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও এঁরা বাংলা কাব্যে অনেক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বৈচিত্র্যের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের নামই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়ে থাকে।
বিশিষ্ট মনীষী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের যে মূল্যায়ন করেছেন তা থেকেই তাঁর কাব্য-বিষয়ে মােটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবি হিসেবেই উল্লেখযােগ্য নহেন, বাংলা কাব্যে একটা বিশিষ্ট প্রভাব-রূপেও তিনি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-কাব্য হইতে অতি আধুনিক কাব্যের যে সুর পরিবর্তন, তাহার মূলে অনেকটা তাহারই প্রভাব। কাব্যে চলতি ভাষা ও কথাভঙ্গী, হাল্কা সুর, দেশ-বিদেশ হইতে আহৃত নানা অপরিচিত শব্দের সুষ্ঠু ও নির্ভীক প্রয়ােগ, নুতন নূতন ছন্দরীতির মাধ্যমে ভাবের সাবলীল, উল্লসিত প্রকাশ, জীবনের বহু নূতন বিভাগে, অনুভূতির বহু নূতন ক্ষেত্রে কাব্যসীমার প্রসার আধুনিক কাব্যের এই সমস্ত প্রবণতা বহুলাংশে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত প্রভাবিত।…আধুনিক কবিতার যে প্রধান লক্ষণ ভাবগভীরতার পরিবর্তে কৌতুহল বিস্তৃতি, কাব্যানুরঞ্জনের স্থলে জীবন-রসের আস্বাদন বৈচিত্র্য, স্তব্ধ ধ্যান-তন্ময়তার স্থলে গতিবেগের উন্মাদনা, প্রথাগত কাব্যরীতির পরিবর্তে সংলাপ-ভঙ্গীর দ্রুত সঞ্চারী ভাবানুগামিতাতাহা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য পরীক্ষা হইতেই প্রধানতঃ উদ্ভূত।”
সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার এখনও যথার্থভাবে হয়নি। কিছু মানুষ তাঁকে ‘ছান্দসিক’ হিসেবে কটাক্ষ করেছেন, আবার অনেকে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন।
প্রধানত কবিরূপে পরিচিত হলেও, সত্যেন্দ্রনাথ গদ্য-রচনাতেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন গদ্যধারায় তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। বিশেষত নানা জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ রচনায় তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় তাঁর বিভিন্ন মৌলিক ও অনুবাদ রচনার সন্ধান পাওয়া যাবে: ‘সবিতা’ (১৯০০), ‘সন্ধিক্ষণ’ (১৯০৫), ‘বেণু ও বীণা’ (১৯০৬), ‘হােমশিখা’ (১৯০৭), ‘তীর্থসলিল’ (অনুবাদ কবিতা, ১৯০৮), ‘তীর্থরেণু’ (অনুবাদ কবিতা, ১৯১০), ‘ফুলের ফসল’ (১৯১১), ‘কুহু ও কেকা’ (১৯১২), ‘জন্মদুঃখী’ (অনুবাদ উপন্যাস, ১৯১২), ‘চীনের ধূপ’ (অনুবাদ প্রবন্ধ, ১৯১২), ‘রঙ্গমন্ত্রী’ (অনুবাদ নাট্য সংগ্রহ, ১৯১৩), ‘তুলির লিখন’ (১৯১৪), ‘মণি মঞ্জুষা’ (অনুবাদ কবিতা, ১৯১৫), ‘অভ্র আবীর’ (১৯১৬), ‘হসস্তিকা’ (‘নবকুমার কবিরত্ব’ ছদ্মনামে রচিত ব্যঙ্গকবিতা, ১৯১৭), ‘বারোয়ারি উপন্যাস’ (৪টি পরিচ্ছেদ, ১৯২১), ‘ডঙ্কানিশান’ (অসমাপ্ত উপন্যাস, ১৯২৩), ‘বেলা শেষের গান’ (১৯২৩), ‘বিদায় আরতি’ (১৯২৪), ‘ধূপের ধোঁয়ায়’ (নাটিকা, ১৯২৯)। কাব্য ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথের যে গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে, সেটি ‘ছন্দ-সরস্বতী’, যা ১৩২৫ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকার বৈশাখ মাসে প্রবন্ধ আকারে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।
পূর্বে বলা হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে ভাবের গভীরতা অপেক্ষা কৌতুক ও কৌতূহলের পরিমাণই ছিল বেশি। বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যে দক্ষতার কারণে, তিনি কাব্যের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্যসাধনে অধিক মনোযোগী ছিলেন। তাই তাঁর কবিতাগুলি হৃদয়ের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারলেও, চক্ষুকর্ণের তৃপ্তি-সাধনে খুবই তৎপর ছিল। ফলে, রসজ্ঞ পাঠকের প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হলেও, সত্যেন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পাঠকের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন। কাব্যের বিষয় হিসেবে কোন না কোন বস্তুকে গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু প্রকৃত কবি সেই বস্তুসত্তাকে রসে পরিণত করেন; অকবির হাতে তা বস্তুপিণ্ডই থাকে। ‘তাজমহল’ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন, যেখানে তাজমহলের বস্তুধর্মের পরিচয় নেই, অথচ সত্যেন্দ্রনাথের ‘তাজ’ কবিতায় সিংহলী নীলা, আরবী প্রবাল, তিব্বতী ফিরোজা পাথরের সমাহারে তাজমহলকে একটি জড়পিণ্ডের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দুইয়ের পার্থক্য হল, দিগন্তবিহারী কল্পনার পর কোমল উত্তাপে বিগলিত করে রবীন্দ্রনাথ যখন লাবণ্য করা অরূপ রতন সৃজনে ব্যস্ত, সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেই বস্তুটিকে রেখাঙ্কনের কৌতূহলে মগ্ন থাকেন। শুধু বস্তুজগত এবং প্রকৃতিজগত নয়, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতির বিভিন্ন কবিতাতেও সত্যেন্দ্রনাথের স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা পুঞ্জীভূত তথ্যের আকার ধারণ করে। বস্তু চিরকাল বস্তুপিণ্ডই থাকে, তা কখনো রসমূর্তি পরিগ্রহ করে না।
সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্র ছন্দ-রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম তিন জাতীয় ছন্দকে সার্থকভাবে ব্যবহার করলেও, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সীমা আরও প্রসারিত করেছেন। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মধ্যে যত প্রকার বৈচিত্র্য সম্ভব, সত্যেন্দ্রনাথ তা সৃষ্টি করেছেন। ইংরেজি, জাপানী, আরবী, ফারসী ভাষার বিচিত্র-ছন্দকেও তিনি একই কাঠামোতে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাতে তাদের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ন রেখেছেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও তাঁর অনুকরণে কিছু লোক কিছু সংস্কৃত ছন্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন এবং সংস্কৃত নিয়মে বাংলা দীর্ঘস্বরে দুই মাত্রা ব্যবহার করেছেন, যা বাংলা উচ্চারণ প্রকৃতির বিরোধী। সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন উচ্চারণ প্রকৃতি অক্ষুণ্ন রেখেই। তাঁর ‘ছন্দ-সরস্বতী’ নামক গ্রন্থটি কাব্যমণ্ডিত ভাষায় রূপক-আকারে রচিত হলেও, বাংলা ছন্দের যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ তাতেই সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়েছে। ছন্দ-বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ দক্ষতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ছন্দের যাদুকর’ অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।
সত্যেন্দ্রনাথের অপর বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে শব্দ-নির্বাচনে। এই বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্র-পন্থী—যে হোক ভাষা কাব্য রস নিয়ে। যথাযথ পরিবেশ এবং উপযুক্ত রস সৃষ্টির জন্য তিনি নির্বিচারে দেশি এবং বিদেশি আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন, পাশাপাশি অপ্রচলিত তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেও অকুণ্ঠ ছিলেন।
বিদেশি শব্দ এবং ছন্দ ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আরবী, মিশরীয়, ফারসী, চীনা, জাপানী বা ইংরেজী কবিতার অনুবাদে এবং অনেক সময় মূল কবিতার ছন্দের অনুবর্তনেও অনুরূপ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: “তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃত্তস্বরূপ আশ্রয় করে স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরব তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ ও নতুন কাব্য।” অনুবাদের এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে!