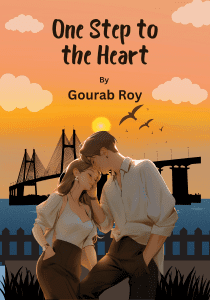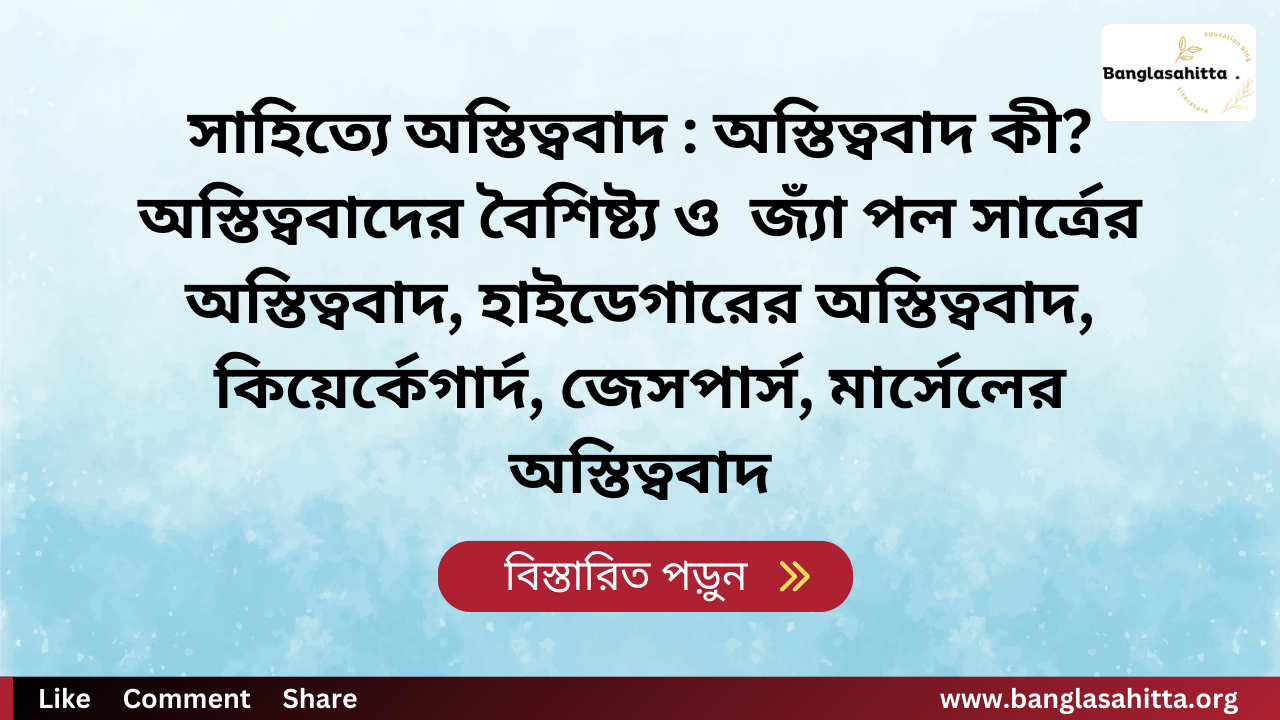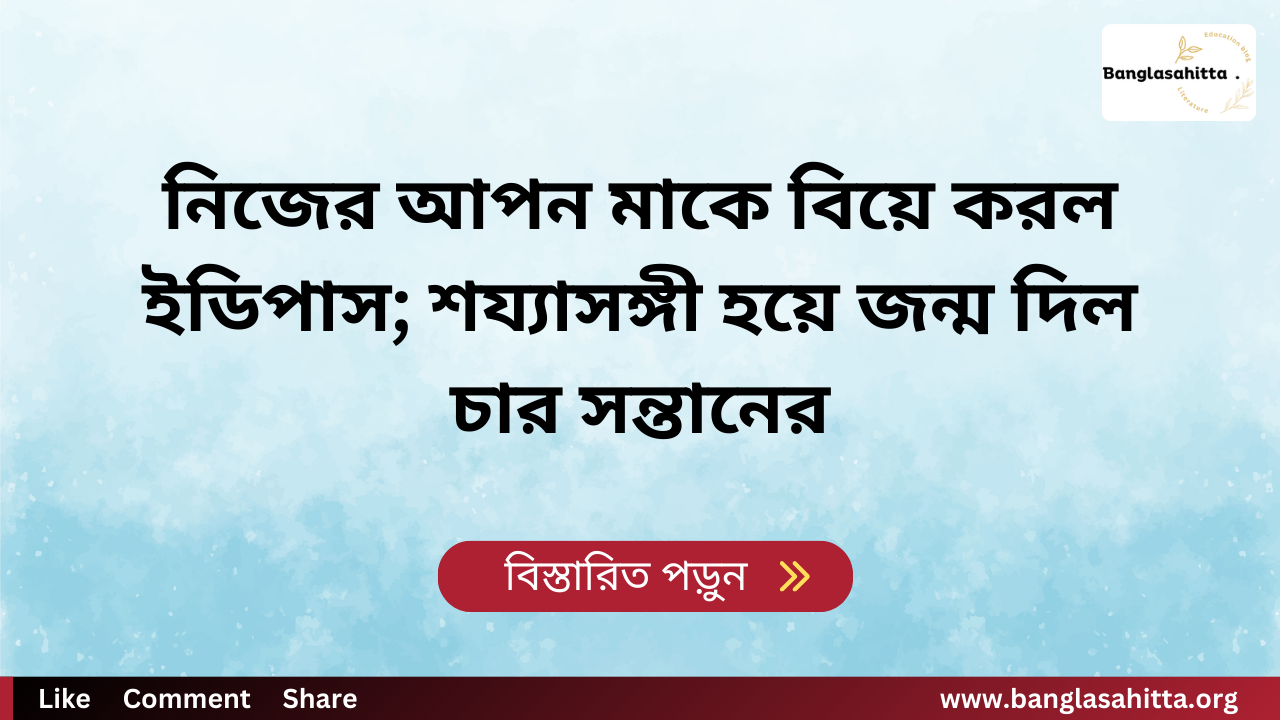মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেছিলেন মধ্যযুগের ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময় বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাস রচনার কোন চল ছিল না। তবুও অনেক সমালোচক মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটিতে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি এযুগে জন্মালে একজন সার্থক ঔপন্যাসিক হতেন। আমাদের আলোচনা করে দেখা দরকার মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণগুলি কতটা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
উপন্যাসের লক্ষণগুলি বিচার করতে গেলে প্রথমেই আসে কাহিনি প্রসঙ্গ। মুকুন্দ চক্রবর্তী চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করলেও একাব্যে একটি কাহিনি আছে এই কাহিনিটি ব্যাধ কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরার কাহিনি। কাব্যটির দেবদেবীর অংশটি বাদ দিলেও কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি হিসাবে কাব্যটি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। আমরা দেখি ধর্মকেতু ও নিদয়ার সন্তান কালকেতু বনে পশু শিকার করে এবং সেই পশুর মাংস, চামড়া, দাঁত প্রভৃতি বিক্রি করে তাদের জীবন চলে। কালকেতুর অত্যাচারে বিব্রত হয়ে পশুরা তাদের আরাধ্যা দেবী চন্ডীর শরণাপন্ন হলে দেবী চন্ডী তাদের অভয় দেন এবং কালকেতুকে ব্যাধ থেকে রাজাতে পরিণত করেন। এইভাবে কাব্যটিতে উপন্যাসের প্রথম লক্ষণ অর্থাৎ কাহিনির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
উপন্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণ চরিত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেব চরিত্র থেকে শুরু করে সকল প্রকার মানব চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এখানে নায়ক এবং নায়িকা হিসাবে কালকেতু ও ফুল্লরা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বুলান মন্ডলের মত ভাল মানুষও আছে। আধুনিক উপন্যাসে যেমন খল চরিত্র থাকে তেমনি এখানে মুরারী শীলও ভাঁড়ুদত্ত খল চরিত্র হিসাবে পরিকল্পিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে পশুদেরও মানব চরিত্রে উত্তরণ ঘটেছে। যখন মুকুন্দের ভালুক বলে—
“উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।”
তখন ভালুক আর ভালুক থাকে না, সে মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই দেখা যায় উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সার্থক চরিত্র চিত্রণ তা প্রধান চরিত্রই হোক বা অপ্রধান চরিত্রই হোক; তার যথেষ্ট সমাবেশ এই কাব্যে আছে।
উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি বিন্যাস। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা প্লট বা কাহিনি বিন্যাসের অপরূপ সমাহার আমরা দেখতে পাই। এখানে কোন ঘটনাই এমনি এমনি ঘটেনি। প্রতিটি কার্যের পিছনেই আছে কোন না কোন কারণ। তাই বলা যায় এখানে কার্যকারণ পরম্পরা সূত্র ঠিকমত মেনে চলা হয়েছে। এই জন্যেই নীলাম্বর ও ছায়া অভিশাপ গ্রস্থ হয়ে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করেছে, ব্যাধ কালকেতু প্রথমে পশুশিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেছে, তারপরে পশুরা দেবীর কাছে নালিশ জানিয়েছে, দেবী তাদের অভয় দিয়েছেন এবং কালকেতুকে আশির্ব্বাদ করে ব্যাধ থেকে রাজায় পরিণত করেছেন। শেষপর্যন্ত রাজা কালকেতু দেবী চন্ডীর পূজা প্রচার করে অভিশাপ মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বর্গে ফিরে গেছে। এইভাবে উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্লট এখানে পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে।
উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবতা। চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি মধ্যযুগের ভক্তির যুগে বসে লেখা। স্বাভাবিকভাবেই এই কব্যে বাস্তবতার অতটা প্রয়োগ অসম্ভব ছিল; কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যক্ষেত্রে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছেন। এই কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে মুকুন্দের আত্মজীবনের পরিচয় অংশ, নরখন্ডের ফুল্লরার বারোমাসের সুখ দুঃখের বারোমাস্যায়, নারীগণের পতিনিন্দায় এবং দেবী চন্ডীর কাছে পশুদের দুঃখ নিবেদন করে ‘পশুগণের গোহারি’ অংশটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত উপায়ে লেখা। এই কাব্যের ব্যাধ কালকেতু, ফুল্লরা, বুলান মন্ডল, ভাডুদত্ত, মুরারী শীল, বনের পশুরা সকলেই বাস্তবধর্মী চরিত্র। এই কারণেই রমেশ চন্দ্র সেন বলেছেন—
“The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature.”
স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি বাস্তব সম্মত ভাবে রচিত।
প্রত্যেকটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই কোন না কোন পটভূমি থাকে, যার উপর ভিত্তি করে ঔপন্যাসিক উপন্যাস গড়ে তোলেন। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারই মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই পূজা প্রচারকে পটভূমি ধরে তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন। আর এখানেই কাহিনি চরিত্র, প্লট, বাস্তবতা সবই প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ পটভূমি এই কাব্যে আছে।
উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশরীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রকাশরীতি দুই রকমের— বর্ণনারীতি এবং সংলাপের রীতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার কাব্যটির আখ্যানভাগ কবিতা আকারে রচনা করায় এখানে প্রকাশ রীতির ক্ষেত্রে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনা রীতি গ্রহণ করেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজন মত সংলাপের রীতিও গ্রহণ করেছেন। যদিও এই দু’টি রীতি যে কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; তবুও উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রকাশ রীতির আলোচনা বেশি আসে। তাই বলা যায় উপন্যাসের এই লক্ষণটিও চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে।
উপন্যাসের মাধ্যমে লেখকের জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দের দর্শন ছিল দেবী চন্ডীর পূজা প্রচার করা; কিন্তু তার চেয়েও বড় দর্শন ছিল মানবিকতার প্রচার। এই কাব্যে আমরা দেখি মুকুন্দ চক্রবর্তী জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে নিজের সাত পুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন ৷ তার এই সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন—
“তৈল বিনা কৈনু স্নান
করিনু উদগ পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।”
কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী কখনোই দুঃখের যন্ত্রনাই ভেঙে পড়েন নি- দুঃখ যন্ত্রনা থেকে নিবারণের পথ খুঁজেছেন। তাই মুকুন্দের নায়ক কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করে বুলান মন্ডলকে আহ্বান করে বলেন-
“শুনো ভাই বুলান মন্ডল।
আইস আমার পুর
সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল।।
আমার নগরে বস
যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিনসন বহি দিও কর।।”
এমনকি মুকুন্দ চক্রবর্তী দরিদ্র ভাঁডুদত্তেরও পুনর্বাসন করেছেন তার কাব্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মত চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে।
এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আধুনিক উপন্যাসের প্রায় সব লক্ষণই সার্থকভাবে পরিস্ফুট। মুকুন্দ চক্রবর্তী মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে কাব্যচর্চা করেছিলেন। সেই সময় ভারতীয় সাহিত্যে তো বহুদূরের কথা বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাসের প্রচলন হয়নি৷ স্বাভাবিকভাবেই মুকুন্দ চক্রবর্তীর দ্বারা উপন্যাস রচনা করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু তিনি চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি যেভাবে রচনা করেছিলেন তা পর্যালোচনা করে সমালোচকের মন্তব্যটি অর্থাৎ মুকুন্দ চক্রবর্তী এযুগে জন্মালে ঔপন্যাসিক হতে পারতেন মেনে নিতেই হয়।