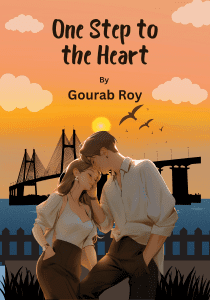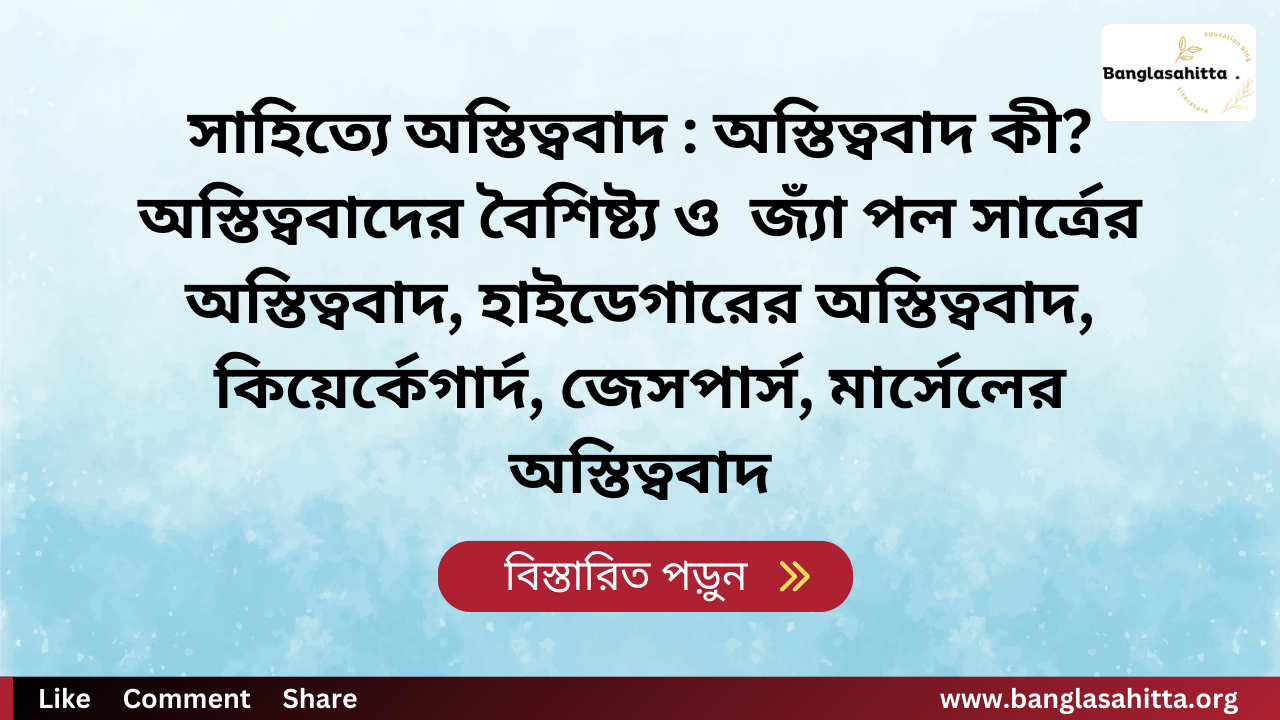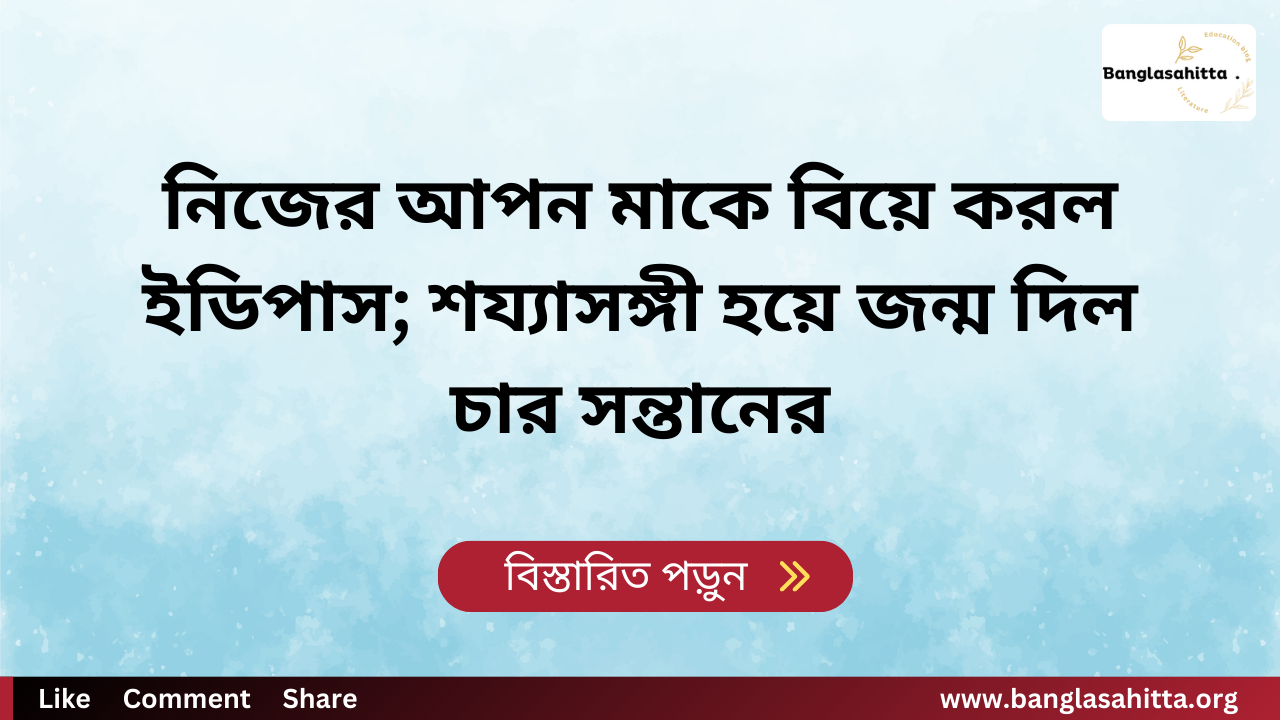এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়; জন্মগ্রহণের পর মৃত্যু অনিবার্য। আমরা যতই প্রিয়জনকে নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধতে চাই, পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য নিয়মে সেই বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। এ কারণে জগতে বেদনা ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের হাহাকার চারপাশে ভেসে যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতায় এই অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে মানবজীবনের করুণ দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে কবির এই ভাবনাকে অভিনব বলা চলে না। তবুও, পুরানো এই সত্যটি কবির কল্পনায় সজীব হয়ে উঠে, যা আমাদের নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। কবিতাটি অভিনব মনে হওয়ার কারণে বিশ্ব ও জীবন সম্পর্কে কবির উপলব্ধির বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। কবি সাধারণ অভিজ্ঞতাকে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করে বিশ্বজগতের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন।
কবিতার শুরুতে একটি সাধারণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পূজার অবকাশে প্রবাসে যাত্রার প্রস্তুতির সময় গৃহিণীর মমতার অভিব্যক্তি অত্যন্ত সাধারণ দৃশ্যকে বেদনার রসে আপ্লুত করেছে। যাত্রার মুহূর্তে প্রবাস যাত্রী শিশুকন্যাটির কাছে বিদায় চেয়েছে। কিন্তু কি ভেবে কে জানে, শিশুটি বলে উঠেছে, ‘যেতে আমি দিব না তোমায়।’ এই স্নেহের দাবি প্রতিনিয়তই এই সংসারে উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে হৃদয়ের এই দাবি তুচ্ছ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত কবিতাটিতে বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু এরপর থেকেই কবিতায় ভিন্ন সুর শুরু হয়েছে। কবিকল্পনা শিশুকন্যার গর্বিত স্নেহবাণীর প্রভাবে জেগে উঠে, বিশ্বের গভীর বেদনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছে। কবির কল্পনায়, সমগ্র বিশ্বই কাব্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসুন্ধরা মাতৃরূপে প্রতিভাত হয়েছে, যিনি স্নেহের বাঁধনে আপন সন্তানদের বেঁধে রাখতে চান—তৃণতরু থেকে জীব সমস্তই তাঁর সন্তান। তবে কিছুই তিনি ধরে রাখতে পারেন না তাঁর সীমাবদ্ধ ভালোবাসার ক্ষমতা দিয়ে। পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রাণধারা প্রলয় সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে, আর এই গতি রোধ করার সাধ্য কারও নেই। স্নেহ ও প্রেমের বন্ধন যত বড়ই হোক, মৃত্যুর কাছে তাকে পরাভব স্বীকার করতেই হয়। এই পরাভবের বেদনা বিশ্বজুড়ে বিষাদ-কুয়াশার আবরণ বিস্তৃত করে। কবির দৃষ্টিতে মাতা বসুন্ধরা এক বিষাদময়ী মাতৃমূর্তিতে ধরা দিয়েছেন—যিনি সৃষ্টি করেন কিন্তু রক্ষা করতে পারেন না।
মানবজীবনের একটি সাধারণ দুঃখময় ঘটনা দিয়ে শুরু কবিতাটি ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী বেদনার বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে পৌঁছে যায়। এই উত্তরণের ফলে কবিতায় বিশ্ব প্রকৃতির দৃশ্য স্থান পেয়েছে, যা বেদনার রসে ভারাক্রান্ত। সংকীর্ণ অর্থে এ মানবজীবনের ট্র্যাজেডি নয়; বরং এই ট্র্যাজেডিকে সমগ্র বিশ্বজীবনের মূলের সঙ্গে যুক্ত করে কবি গভীরতর জীবন রহস্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মানবজীবনের বিচ্ছেদ-বেদনা বিশ্বজীবনের পটে সংস্থাপিত হওয়ায় এটি ব্যাপকতা ও মহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।
বিশ্বজগতে নিত্য প্রবহমানতা যেমন সত্য, স্থিতির আকাঙ্ক্ষাও তেমনি সত্য। স্নেহের প্রেমের সম্পদকে চিরকাল রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা জীবনের সহজাত। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয় না; গতির চলমানতার কাছে পরাভব স্বীকার করে। হৃদয়ের করুণ কোমল বাসনাগুলি প্রতিমুহূর্তে বিফল হচ্ছে, ভালোবাসার বন্ধন স্খলিত হয়ে যাচ্ছে। জীবনের এই বেদনার দিকটাই কবিতায় বিশেষভাবে কবি-কল্পনার অবলম্বন। কবি জগৎ ও জীবনের প্রবহমানতা এবং পরিবর্তনশীলতার সত্যকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁর ভাবনা ও কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছে গতির আঘাতে বিচূর্ণিত ভালোবাসার জন্য দুঃখবোধ। তাই তিনি পুরো বিশ্বকে বিষাদাচ্ছন্নরূপে দেখিয়েছেন। বিশেষভাবে কবিতার শেষ অংশে বেদনাবিধূর শিশুকন্যার সঙ্গে বিষাদময়ী ধরিত্রীকে একাকার করে ফেলেছেন। মাতা বসুন্ধরার উদাসিনী বিষাদ-মূর্তির বর্ণনায় কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতির ওপরে মানবীয় ভাব আরোপের নৈপুণ্যের দিক থেকে কবিতাটি আশ্চর্য সফল। বিদায়মুহূর্তে শিশুকন্যার স্নান মুখখানির বিষাদময়তা কবি অনায়াসে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির ওপরে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। চিরদিনের পরিচিত পৃথিবী কবি-কল্পনার মাধ্যমে নতুনরূপে প্রতিভাত হয়।
অপ্রতিরোধ্য নিয়তির আঘাতে কাতর শোকার্ত ধরিত্রীমাতার উদাসিনী মূর্তি পাঠকের মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। প্রাত্যহিক সংসারের যাত্রার মধ্যে বিশ্বজীবনের এক গভীর রহস্য প্রতিফলিত হয়। তবে, সংসারের অলঙ্ঘনীয় এই নিয়ম, মানবাত্মার এই চিরন্তন ট্র্যাজেডি কবিকে নৈরাশ্য ও নিস্পৃহতার দিকে কখনও ঠেলে দেয়নি। বরং এই কঠোর নির্মম অনুশাসনকে স্বীকার করেই কবির মনে এক তীব্র পৃথিবী-প্রেম জেগে উঠেছে, যা কবিতাটির প্রধান মর্মবাণী।