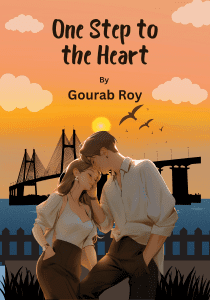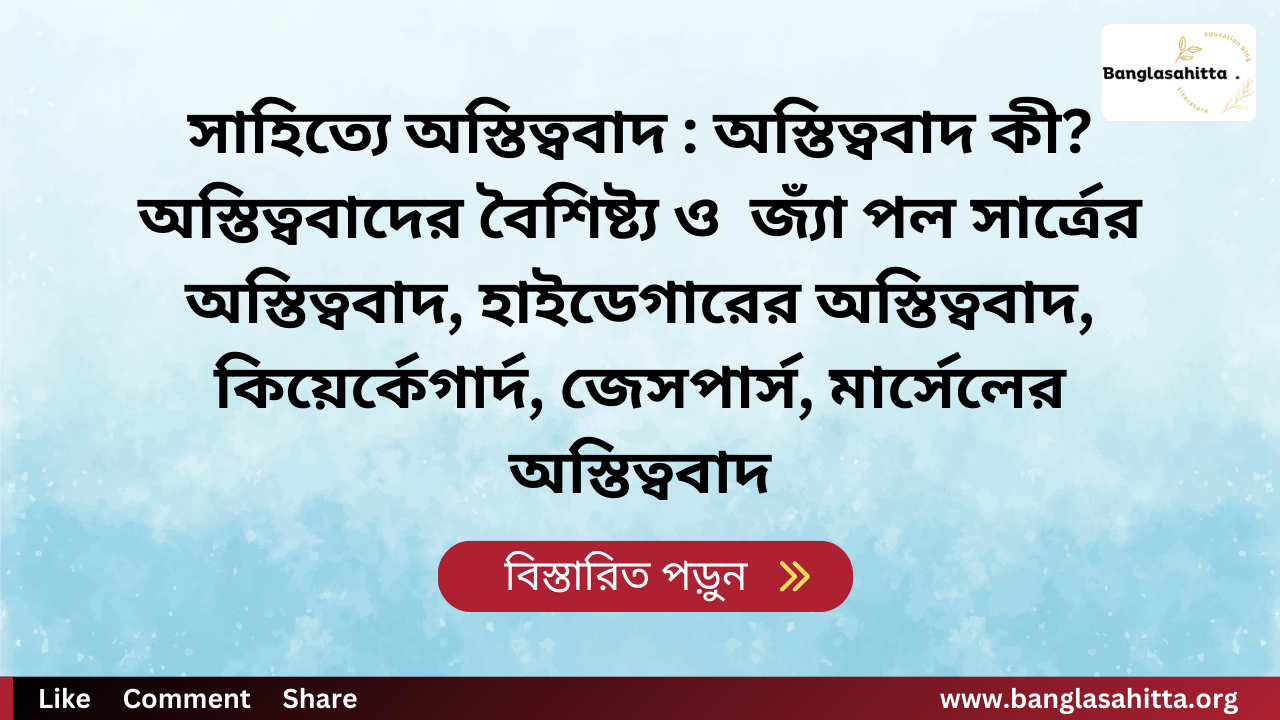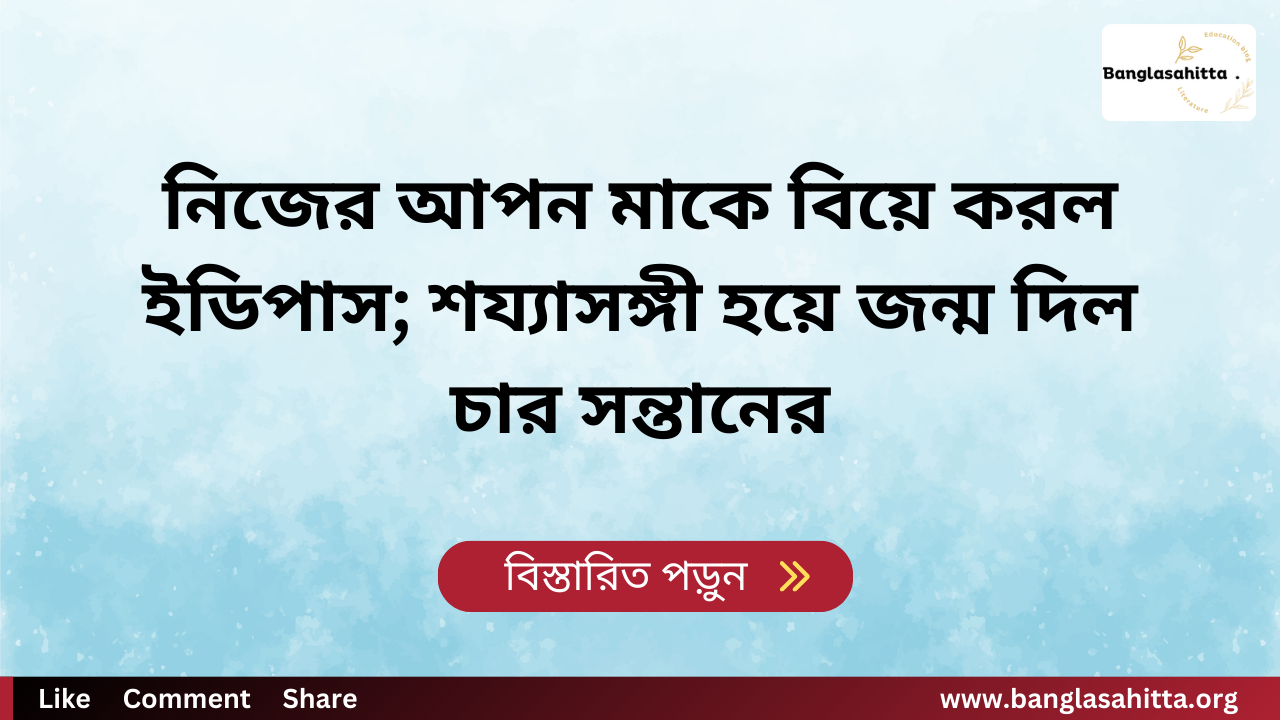বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) দুঃখবাদী কবি হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল সৃজনশীলতায় বাংলা সাহিত্য যখন দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন রবিমণ্ডলকে অতিক্রম করে যে ক’জন কবি স্বকীয় দীপ্তি বিচ্ছুরিত করতে পেরেছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মোহিতলাল, নজরুল, এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রগতি-কল্লোল-কালিকলমের তরুণ কবিরা যখন রবীন্দ্র-প্রভাব উত্তরণের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখন মোহিতলালের ভোগবাদী চেতনা, নজরুলের মুক্ত যৌবন, এবং যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও জড়বাদ নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের সদা পরিবর্তনশীল ও আত্মপ্রসারী কবিত্ব এই নবীন কবিদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। তারা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার তীব্র বাসনায় একেকজন নিজেকে এক একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তির মধ্যে বন্দী করে স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিলেন। এই সূত্রেই মোহিতলাল দেহবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন আর যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদের। দুঃখবাদী দর্শনের পুনরাবৃত্তিই যতীন্দ্রনাথের প্রধান গুণ এবং প্রধান ত্রুটি।
১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কবিতা রচনা শুরু করলেও যতীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মরীচিকা’ (১৯২২) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল ‘মরুশিখা’ (১৯২৭), ‘মরুমায়া’ (১৯৩০), ‘সায়ম’ (১৯৪১), এবং ‘ত্রিযামা’ (১৯৪৮)। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ‘নিশান্তিকা’ (১৯৫৭)। এই কাব্যগ্রন্থে তার কবিমানসের বিবর্তনের কিছু চিহ্ন ধরা পড়ে।
যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-বিরোধী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই তিনি জীবনদর্শনের দিক থেকে রবীন্দ্র-বিরোধী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শাশ্বত সৌন্দর্যের পূজারী, ঔপনিষদিক অমৃততত্ত্ব বা আনন্দবাদের প্রতি তার আস্থা ছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে দেখেছেন দুঃখময়। দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, চলা, এবং পরিণাম দুঃখসর্বস্ব বলেই তার দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে।
প্রকৃতি সৌন্দর্যের স্তুতি কবিগণের এক প্রিয় কাব্যবিষয়। সেই প্রকৃতি কখনও লাবণ্যময়ী। ষড়ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির বিচিত্র রূপলীলা চিরকালই কবিগণকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সংশয়বাদী যতীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারলেন না। প্রকৃতির রূপলাবণ্যের বাহ্যিক আয়ােজন তার চোখে ধরা দিল সর্বনাশা প্রলােভন বা প্রকৃতির টোপ’ হিসাবে। যে বিধাতাপুরুষকে আমরা লীলাময় ও করুণাময় বলে জানি, অসলে তিনি প্রকৃতির সুন্দর রূপের টোপে গেঁথে নিরীহ মানুষকে অনন্ত দুঃখ-জলধিতে যন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। এদিক দিয়ে তিনি মূলত অ্যাণ্টি-রােম্যান্টিক। তাই দুঃখবাদী কবিতায় প্রকৃতির এই নির্মমতার পরিচয় দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন—
‘বজ্রে যে জনা মরে
নব ঘনশ্যাম শােভার তারিফ সে বংশে কেবা করে?’
প্রকৃতির এই মােহসঞ্চারী রুপের প্রতি তীব্র শ্লেষ উচ্চারিত অন্যত্র, যেখানে তিনি সন্ধ্যায় মায়াময় রূপকে মােহময়ী বারাঙ্গনার সঙ্গে তুলনা করেছেন—
‘বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘে হাসে পশ্চিমে আনমনা
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙ্গিন বারাঙ্গনা।’
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাই সৌন্দর্যের অন্তরালে মনুষ্যজীবনের পক্ষে একান্তভাবেই অন্তঃসারশূন্য হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে কবির সংশয়ী দৃষ্টিতে—
‘এ ব্রহ্মান্ডুঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।’
মেঘ সমুদ্র থেকে বারিবিন্দু চুরি করে অনিয়মিত বর্ষণে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে। অথচ যেখানে বর্ষণের প্রয়ােজন। সেখানে প্রকৃতির করুণা এক বিন্দুও ঝরে পড়ে না। তাই কবির জিজ্ঞাসা—
‘একখানা মেঘ ধার দিতে পারাে গােবি সাহারার বুকে!’
ক্ষুধা ও প্রয়ােজনের মানদণ্ডে পৃথিবীকে পরিমাপ করতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছিলেন প্রেমকে। বলেছিলেন—‘প্রেম বলে কিছু নাই/চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই। বিজ্ঞান বলে জড় ও চেতনের অবিরাম সংঘর্ষ চলছে। জড় থেকেই চেতনার জন্ম ও লয়। তাই প্রেম তার কাছে অর্থহীন। বস্তুবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ টমাস হার্ডির মধ্যে নরনারীর প্রেম ও মিলনের আনন্দকে স্বীকার করতে পারেন নি। কেননা জীবনের পরিসমাপ্তিতে আছে মৃত্যু। মৃত্যুতে প্রেম ব্যর্থ হয়ে যায়—
‘মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারােটার বেশি রাতি।’
তাছাড়া প্রেমের মিলনানন্দ বহু মৃত্যুর মূল্য কেনা বলেও অনুভব করেছেন যতীন্দ্রনাথ। মিলনের বাসর শয্যার পথে বিছানাে পদ্মের পাপড়ি, ছড়িয়ে দেওয়া আতরের সুগন্ধ এই সব কিছু সঙ্গে মেশানাে অসংখ্য মৃত্যুর ইতিহাস। কবির তাই প্রশ্ন—
‘ভরেছ আতরদানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি ছানি।’
অথবা
‘কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা-
সদ্য ছিন্ন শিশু-কুসুমের কচিমুণ্ডের মালা।’
‘মরীচিকা’ কাব্যের ‘ঘুমের ঘােরে’ কবিতায় কবি ঈশ্বরের প্রতিও হয় অবিশ্বাস, নয় ঘৃণা জ্ঞাপন করেছেন। পৃথিবীকে গ্লানিমুক্ত করতে যুগে যুগে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কাহিনী তার কাছে মিথ্যা অথবা ব্যর্থ। মহাপুরুষ বা অবতারগুণের আশ্বাসবাণীও অন্তঃসারশূন্য। খৃষ্টের পুনরাবির্ভাবের পরেও গ্লানিময় পৃথিবী অপরিবর্তিতই থেকে যায়—
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না এক চুল;
ভগবান চান আমাদের শুভ-একথা হইল ভুল।
প্রকৃতি ও প্রেমের মতাে ঈশ্বরের তীব্র সমালােচনা করার ফলে ঈশ্বর ক্রদ্ধ হলেও তিনি অপারগ—
‘তিক্ত সত্যে চটে যান যদি ভক্তের ভগবান,
মােরে ছেড়ে তিনি বাকি সাধুদের করুন পরিত্রাণ।’
কিন্তু রবীন্দ্রবিরােধিতা ও প্রকৃতি-প্রেম-ঈশ্বরের বিপক্ষতা করলেও যতীন্দ্রনাথের অন্তরে ফল্গুধারার মতাে প্রবাহিত প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষুধা, পার্থিব যন্ত্রণা ভােগ করেই মূলত তিনি প্রবল বিক্ষোভে বিরুদ্ধচারী হয়েছেন বলে মনে হয়। তবে প্রথম তিনটি মরুচিহ্নিত কাব্যগ্রন্থের পরে সম্ভবত মরূদ্যানের সন্ধান পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তাই পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে তাঁর মানস বিবর্তনের পথরেখাটি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। ‘সায়ম’ কাব্যগ্রন্থ থেকে মরু-বন্দনার বদলে শুরু হয় প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরের সন্ধান। ‘বসন্ত’ কবিতায় উদরের ক্ষুধাকে অস্বীকার না করেও কবি বলেন- ‘ফেনায়ে উপছি পড়ে হৃদয়ের সুধাপাত্র মাের’। আরাে বলেন যে, নিদাঘের দাবদাহ সহ্য করার জন্যই হয়ত প্রয়ােজন ‘পদ্মবনের গন্ধবহ’। ‘দেখা দাও’ কবিতায় কবি স্বীকারােক্তি করেন যে, তাঁর মরুপ্রীতির কারণ চিরসুন্দরের প্রতি সুতীব্র অভিমান। ‘ত্রিযামা’ গ্রন্থের ‘হেমস্ত সন্ধ্যায়’ কবিতাতেও কবি প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। এমন কি পূর্বের প্রকৃতি বিদ্বেষের জন্য এখানে আক্ষেপও ধ্বনিত।
প্রেম সম্পর্কেও কবির মনােভাবের পরিবর্তন ঘটে মরু-কাব্যত্রয়ীর পর। ‘সায়ম’ কাব্যের ‘যন্ত্রহীন’, ‘ত্রিযামা’র ‘ভােরের স্বপ্ন’, ‘প্রত্যাবর্তন’, ‘সমাধান’, ‘নির্বাসন’ প্রভৃতি কবিতায় সেই প্রেমস্বপ্নেরই অনুধ্যান। ‘মন্ত্রহীন’ কবিতায় কবি স্ত্রীকে সম্বােধন করে জন্মান্তরীণ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। দেহকে ছেড়ে তিনি এখন দেহাতীতের সন্ধান করেন, কারণ তিনি জেনেছেন, মৃত্যুই শেষ কথা নয়। ‘ভােরের স্বপ্ন’ কবিতায় কবি স্মরণ করেছেন প্রথম ভালােবাসার কথা। যে কবি একদা ‘প্রেম বলে কিছু নাই’ বলে বলিষ্ঠ ঘােষণা করেছিলেন, তিনিই ‘সমাধান’ কবিতায় প্রৌঢ়ত্বের উত্তাপে দগ্ধ হয়ে অনুভব করেছেন—
‘বৈশাখী তারপে তুলসীর ঝারি
যে সিনান মােরে করে মরুচারী
যে-দাব দহনে বাহন করিয়া এ জীবন পােড়ালেম,
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মাের প্রেম।’
জীবনের সায়াহ্নে বসে প্রেম ও সুন্দরকে আবার ক্ষণেকের জন্য হলেও পেতে চেয়েছেন। তিনি—‘পেলে ক্ষণতরে বুকে টেনে তারে আরবার হারাতেম।’ একদিন যাকে পৌরুষের দীপ্ত তেজে অস্বীকার করেছিলেন, আজ তিনি তারই জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—
‘যারে বলেছিনু নাই
চেতনার কুলে বসি চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।’
সকল দুঃখের উৎস ঈশ্বর বলে ঈশ্বরকে তিনি প্রথমাবধি অস্বীকার করতে চাইলেন। বস্তুত যতীন্দ্রনাথ ঈশ্বর-অবিশ্বাসী কবি নন, কেননা নিঃস্ব, রিক্ত, নীলকণ্ঠে শিব বেদনার সাযুজ্যে তাঁর ঈশ্বর। সাংসারিক যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য যেমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, তেমনি কবিও নিদ্রার কোলে আচ্ছন্ন থাকার অভিনব মহৌষধ আবিষ্কার করেছেন—
‘এ ভব রােগের নব চিকিৎসা আমার ঘুমিওপ্যাথি।’
‘শিবন্তোত্র’, ‘কচি ডাব’, ‘ভাঙা গড়া’ প্রভৃতি কবিতায় কবির বিশিষ্ট ঈশ্বর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষ করে ‘কচি ডাব’ কবিতার বৃদ্ধ ডাব-বিক্রেতার মধ্যে শিবের দর্শন এক মহৎ মানবীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত।যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একান্তভাবেই মানবতাবাদী। মানব-প্রীতির তীব্রতাবশতই তিনি ভাববাদী দর্শনের ছলনাগুলিকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। নজরুল যেমন মানুষের জন্য সত্য-শিব-সুন্দরের পথকে কন্টকমুক্ত করতেই হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী কবি, যতীন্দ্রনাথও তেমনি মানব-প্রীতির প্রেরণাতেই জড়বাদী ও দুঃখবাদী। এই মানবতাবাদের প্রেরণাতেই কৃষকের হাতের কাস্তে শিবের শিরােদ্ধৃত চন্দ্রকলার সঙ্গে তার চেতনায় এক হয়ে যায়। শিবস্তুতির মধ্য দিয়ে বস্তুত তিনি মানুষের গানই গেয়েছেন। মর্ত্য হইতে বিদায়’ কবিতায় তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠতার জয়গান করে বলেছেন—
‘নর চিরদিন নরই যেন থাকে,
হয় নাকো নারায়ণ।’
রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির চেষ্টা যতীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবিদের কাছে বরণীয় করে তুললেও বস্তুত যতীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কবি জীবনের দ্বিতীয় পর্বে প্রকৃতি সৌন্দর্য, প্রেম ও ঈশ্বরের মতাে রবীন্দ্রনাথকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ‘নিশাস্তিকা’ গ্রন্থের ‘দেখা দাও’ কবিতায় তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত অন্তর্যামীর কল্পনা করেছেন। তবু বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখার বিশেষত্ব যতীন্দ্রনাথ আজও উল্লেখযােগ্যভাবে আলােচিত। বিশিষ্ট ভাববস্তুর সঙ্গে তীব্র শ্লেষ ও অমােঘ শাণিত ভায়ার মেলবন্ধনে যতীন্দ্রনাথের কবিতা ইস্পাতের তরবারীর মতােই উজ্জ্বল।